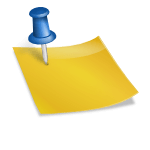ইতিহাস কখনো কখনো কিছু মানুষকে বেছে নেয়—যাদের জীবন শুধু ব্যক্তিগত থাকে না, সময়ের ভার তাদের কাঁধে এসে পড়ে। জিয়াউর রহমান ছিলেন তেমনই একজন মানুষ। তাঁর জীবন কোনো সরল রেখায় চলেনি; তা ছিল বাঁক, সংঘাত, নীরবতা আর হঠাৎ সিদ্ধান্তে ভরা এক দীর্ঘ যাত্রা। সৈনিকের শৃঙ্খলা, বিপ্লবীর সাহস আর রাষ্ট্রনায়কের দায়িত্ব—এই তিনটি সত্তা একসঙ্গে বহন করেছেন তিনি।
১৯৩৬ সালের ১৯ জানুয়ারি। উত্তরবঙ্গের মাটি, বগুড়ার গাবতলী উপজেলার বাটকামারী গ্রাম। এই মাটির বুকেই জন্ম নিল এক শিশু—যে তখন জানত না, ভবিষ্যতে একটি দেশের ইতিহাস তার নামের সঙ্গে জড়িয়ে যাবে। তাঁর পিতা মনসুর রহমান ছিলেন সরকারি কর্মকর্তা—শৃঙ্খলা ও দায়িত্ববোধ ছিল পারিবারিক ঐতিহ্য। শৈশব থেকেই জিয়াউর রহমানের জীবন ছিল সংযত, পরিমিত, দৃঢ়। আবেগের চেয়ে দায়িত্ব তাঁর কাছে বড় হয়ে উঠেছিল খুব তাড়াতাড়ি।
শিক্ষাজীবনে তিনি ছিলেন নীরব, কিন্তু গভীর মনোযোগী। কলকাতা, করাচি—সময় ও ভূগোল বদলেছে, কিন্তু তাঁর ভিতরের মানুষটি বদলায়নি। পাকিস্তান মিলিটারি একাডেমিতে যোগ দিয়ে তিনি যে পথ বেছে নিলেন, তা তাঁকে রাষ্ট্রের শক্ত কাঠামোর ভেতরে নিয়ে গেল। সেনাবাহিনীতে কমিশনপ্রাপ্ত জিয়াউর রহমান ছিলেন একজন পেশাদার সৈনিক—নির্দেশ মানতে জানতেন, কিন্তু অন্যায়ের কাছে মাথা নত করতে জানতেন না।
১৯৭১ সাল। মার্চ মাস। ইতিহাসের সবচেয়ে অন্ধকার রাতগুলো তখন বাংলার আকাশে নেমে এসেছে। ঢাকায় গণহত্যা শুরু হয়েছে, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান গ্রেপ্তার। চারদিকে বিভ্রান্তি, আতঙ্ক, দিশাহীনতা। ঠিক তখনই চট্টগ্রামে এক বাঙালি অফিসার নিজের ভেতরের দ্বন্দ্বের শেষ সিদ্ধান্ত নিলেন। পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর পোশাক তখনো তাঁর শরীরে, কিন্তু আত্মা বিদ্রোহ করে উঠেছে।
২৬ মার্চ। কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র। একটি ক্ষীণ মাইক্রোফোন, চারপাশে মৃত্যুর আশঙ্কা। তবু কণ্ঠে কোনো কম্পন নেই। তিনি বললেন—
বাংলাদেশ স্বাধীন।
তিনি নিজের নাম উচ্চারণ করলেন না ইতিহাসে জায়গা করে নেওয়ার জন্য; বললেন জাতিকে পথ দেখানোর জন্য। এই ঘোষণা ছিল শুধু রাজনৈতিক নয়—এটি ছিল এক সৈনিকের নৈতিক বিদ্রোহ।
এরপর শুরু হয় তাঁর জীবনের সবচেয়ে বিপজ্জনক অধ্যায়—মুক্তিযুদ্ধ। জিয়াউর রহমান যুদ্ধকে দেখেছিলেন দায়িত্ব হিসেবে, আবেগ হিসেবে নয়। তিনি সেক্টর কমান্ডার হন, পরে গঠন করেন জেড ফোর্স—যা ছিল মুক্তিযুদ্ধের প্রথম নিয়মিত ব্রিগেড। সীমিত অস্ত্র, অপ্রতুল রসদ, কিন্তু অদম্য ইচ্ছাশক্তি। পাহাড়, নদী, সীমান্ত—সব জায়গায় তাঁর নেতৃত্বের ছাপ পড়ে।
তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে সামনে দাঁড়াতেন। নির্দেশ দিতেন কম, উদাহরণ সৃষ্টি করতেন বেশি। মুক্তিযোদ্ধারা তাঁকে দেখত—একজন অফিসার নয়, একজন আশ্রয় হিসেবে। যুদ্ধের দীর্ঘ নয় মাস তাঁকে বদলে দেয়—আরও কঠিন, আরও স্থির, আরও নিঃশব্দ করে তোলে।
স্বাধীনতার পর দেশ পেল পতাকা, কিন্তু হারাল স্থিতি। নতুন রাষ্ট্রের ভেতর শুরু হলো অস্থিরতা, ক্ষমতার দ্বন্দ্ব, বিশ্বাসভঙ্গ। জিয়াউর রহমান আবার ফিরে এলেন—এবার যুদ্ধক্ষেত্র থেকে নয়, রাষ্ট্রের সংকটের ভেতর দিয়ে। ১৯৭৫ সালের রাজনৈতিক পরিবর্তনের পর তিনি ধীরে ধীরে ক্ষমতার কেন্দ্রে উঠে আসেন। এই উত্তরণ ছিল সহজ নয়, ছিল বিতর্কিত, কিন্তু ছিল অনিবার্য।
১৯৭৭ সালে তিনি রাষ্ট্রপতি হলেন। রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে তাঁর ভাষা ছিল সংক্ষিপ্ত, দৃষ্টি ছিল বাস্তবমুখী। তিনি “বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদ” ধারণা সামনে আনলেন—যা জাতির পরিচয়কে নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত করল। বহুদলীয় গণতন্ত্র চালু হলো। তিনি চেয়েছিলেন রাজনীতির ভেতর শৃঙ্খলা আনতে, অর্থনীতিতে আত্মনির্ভরশীলতা গড়ে তুলতে।
গ্রাম তাঁর কাছে ছিল উন্নয়নের কেন্দ্র। কৃষি, খাদ্য উৎপাদন, খাল খনন—এসব তাঁর রাজনীতির নীরব স্তম্ভ। আন্তর্জাতিক অঙ্গনে তিনি বাংলাদেশকে পরিচিত করালেন একটি দায়িত্বশীল রাষ্ট্র হিসেবে। দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে সহযোগিতার স্বপ্ন দেখলেন—যার বীজ থেকে পরে জন্ম নেয় আঞ্চলিক উদ্যোগ।
কিন্তু ইতিহাস নির্মম। ১৯৮১ সালের ৩০ মে, চট্টগ্রামে, এক ব্যর্থ সামরিক অভ্যুত্থানে জীবন থেমে যায় এই সৈনিক-রাষ্ট্রপতির। কোনো দীর্ঘ বিদায় নয়, কোনো শেষ বক্তৃতা নয়—হঠাৎ নেমে আসে নীরবতা।

মৃত্যুর পর তিনি হয়ে ওঠেন “শহীদ রাষ্ট্রপতি”। কিন্তু জিয়াউর রহমান শুধু একটি উপাধি নন। তিনি এক প্রশ্ন—ক্ষমতা কী, দায়িত্ব কী, আর ইতিহাস কাকে বেছে নেয়?
জিয়াউর রহমানের জীবন আমাদের শেখায়—সব বীর উচ্চকণ্ঠ হয় না। কেউ কেউ নীরবে সিদ্ধান্ত নেয়, আর সেই সিদ্ধান্তই একটি জাতির গতিপথ বদলে দেয়।